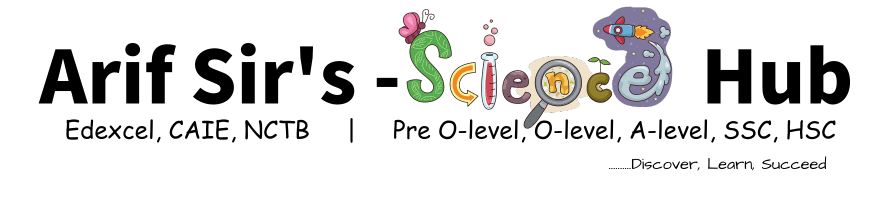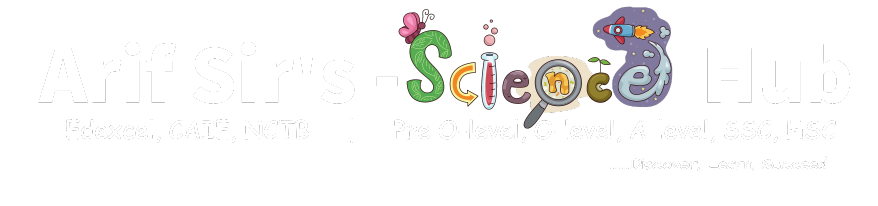উদ্ভিদে সমম্বয় : জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কাজের মাধ্যমে দেহের সকল
কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে সমম্বয় বলা হয়। উদ্ভিদ জীবনে বিভিন্ন স্বতন্ত্র শারীরবৃত্তীয়
কর্মকান্ডের মাঝেও সমম্বয় রয়েছে। একে উদ্ভিদে সমন্বয় বলা হয়। একটি উদ্ভিদের জীবনকালে সময়ের সাথে সামঞ্জস্য
রেখে জীবন চক্রের পর্যায়গুলো যেমন- অঙ্কুরোদগম, বৃদ্ধি ও বিকাশ, পুষ্পায়ন, ফল সৃষ্টি, বার্ধক্যপ্রাপ্তি, সুপ্তাবস্থা, চলন
ইত্যাদি একটি নিয়মে আবর্তিত হয়। পর্যায়গুলোতে আবহাওয়া ও জলবায়ুজনিত প্রভাবকগুলোর প্রভাবও লক্ষ করা যায়।
প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিদের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ স্বতন্ত্র, জটিল ও চলমান হলেও অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বিশেষ নিয়ম মেনে
চলে। এদের একটি কাজ অপর কোন কাজকে বাঁধা প্রদান করে না।
ফাইটোহরমোন : উদ্ভিদদেহে উৎপাদিত হয় এক বিশেষ ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ। এর প্রভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও
বিকাশ ঘটে এবং বিভিন্ন অঙ্গের সৃষ্টি হয়। জৈব পদার্থটি উদ্ভিদের সকল কাজকেই নিয়ন্ত্রণ করে। এ পদার্থকে হরমোন বা
প্রাণরস বলা হয়। এ হরমোনটি উদ্ভিদদেহে তৈরি হয় ও অবস্থান করে বিধায় একে ফাইটোহরমোন বলা হয়। একে উদ্ভিদ
বৃদ্ধিকারক রাসায়নিক বস্তুও বলা হয়। অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের মতে এগুলো উদ্ভিদের কোষে উৎপাদিত হয়ে উৎপত্তিস্থল
থেকে বাহিত হয়ে দূরবর্তী স্থানের কোষ বা কলাসমূহের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। উদ্ভিদের প্রতিটি কোষই হরমোন উৎপন্ন
করতে সক্ষম। এরা কোন পুষ্টি দ্রব্য নয় তবে ক্ষুদ্র মাত্রায় উৎপন্ন হয়ে কোষের ভিন্নতা সৃষ্টি ও দেহের উন্নয়নে ভূমিকা
রাখে।
ফাইটোহরমোনের নাম : উদ্ভিদে যে সব হরমোন পাওয়া যায় সেগুলো হলো অক্সিন, জিবেরেলিন, সাইটোকাইনিন,
অ্যাবসিসিক অ্যাসিড এবং ইথিলিন।
উল্লিখিত এসব হরমোন ছাড়াও উদ্ভিদে আরও কিছু হরমোন রয়েছে যাদের আলাদা করা বা শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।
এদেরকে পস্টুলেটেড হরমোন
বলা হয়। এরা প্রধানত উদ্ভিদের ফুল ও জনন সংশ্লিষ্ট অঙ্গের
বিকাশে সহায়তা করে। এদের মধ্যে ফ্লোরিজেন এবং ভার্নালিন প্রধান। ফ্লোরিজেন পাতায় উৎপন্ন হয় এবং তা পত্রমূলে
স্থানান্তরিত হয়ে পত্রমুকুলকে পুষ্পমুকুল হিসেবে রূপান্তরিত করে এবং উদ্ভিদে ফুল ফুটাতে সাহায্য করে।
উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব : উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ বিকাশের ক্ষেত্রে আলো ও উঞ্চতার প্রভাব লক্ষণীয়। এর
ফলে বিভিন্ন সংশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান উৎপন্ন হয়। ফলে নতুন অঙ্গের সৃষ্টি হয়। কারও কারও মতে,
আলোর উপস্থিতিতে অক্সিন হরমোন নিষ্ক্রিয় হয়। ফলে অন্ধকারে অক্সিনের ঘনত্ব বাড়ে। কেউ কেউ আবার মনে করেন যে,
আলোর প্রভাবে অক্সিন আলোর দিক থেকে অন্ধকারের দিকে চলে যায়। ফলে তুলনামূলক অন্ধকার দিকের কোষগুলো
আলোকিত অংশের কোষগুলো অপেক্ষা বৃদ্ধি পায়। অন্ধকার দিকের কোষগুলো বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্ভিদটি আলোর দিকে বেঁকে
যায়।
ভ্রƒণমূল বা ভ্রƒণকান্ডের অগ্রাংশ অভিকর্ষের উদ্দীপনা অনুভব করতে পারে। একে অভিকর্ষ উপলব্ধি বলা হয়। অভিকর্ষণের
ফলে কোষের উপাদানগুলো নিচের দিকে স্থানান্তরিত হয়। এদের চাপ পার্শ্বীয় কোষের প্রাচীরে পড়ে তাই অভিকর্ষণীয় চলন
দেখা যায়।
উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ বিকাশের ক্ষেত্রে আলো ও উঞ্চতার প্রভাব বেশ লক্ষণীয়। এ সকল উদ্দীপনার ফলে বিভিন্ন সংশ্লেষণ
পদ্ধতির মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান উৎপন্ন হয়ে নতুন অঙ্গের সৃষ্টি করে এবং কোষের উপাদানগুলো নিচের দিকে
স্থানান্তরিত হয়। চন্দ্রমল্লিকা একটি স্বল্প দিবা দৈর্ঘ্যরে উদ্ভিদ।
আলো এবং অন্ধকার এর দৈর্ঘ্যরে ভিত্তিতে পুষ্পধারী উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস : উদ্ভিদে আলো-অন্ধকারের ছন্দকে
বায়োলজিক্যাল ক্লক বলা হয়। উদ্ভিদের আলো-অন্ধকারের ছন্দের উপর ভিত্তি করে পুষ্পধারী উদ্ভিদকে তিন ভাগে ভাগ
করা হয়। যথা-
স্বল্প দিবা দৈর্ঘ্যরে উদ্ভিদ : যে সব উদ্ভিদে পুষ্পায়নে দৈনিক গড়ে ৮-১২ ঘণ্টা আলো প্রয়োজন। যেমন- সয়াবিন, আলু,
ইক্ষু, তামাক, শিম, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া ইত্যাদি।
দীর্ঘ দিবা দৈর্ঘ্যরে উদ্ভিদ : পুষ্পায়নে দৈনিক গড়ে ১২-১৬ ঘণ্টা আলো প্রয়োজন হয়। যেমন- পালংশাক, আফিম, ভুট্টা,
যব, লেটুস, ঝিঙা ইত্যাদি।
আলোক নিরপেক্ষ উদ্ভিদ : পুষ্পায়নে আলো কোনও প্রভাব ফেলে না। যেমন- টমেটো, কার্পাস, আউশ ধান, শসা, সূর্যমুখী
ইত্যাদি।
উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পুষ্পায়নে আলোর ন্যায় তাপ ও শৈত্যের প্রভাব রয়েছে। দেখা গেছে অনেক উদ্ভিদের অঙ্কুরিত বীজকে
শৈত্য প্রদান করলে তাদের ফুল ধারণের সময় এগিয়ে আসে। শৈত্য প্রদানের মাধ্যমে উদ্ভিদের ফুল ধারণকে ত্বরাম্বিত
করার প্রক্রিয়াকে ভার্নালাইজেশন বলা হয়। উদ্ভিদে পুষ্প সৃষ্টিতে উঞ্চতার প্রভাব বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন। বসন্তকালে
গম লাগালে ফুল আসতে বহু দেরি হয়। কিন্তু বীজ রোপনের পর ২০
-৫
০
উষ্ণতা প্রয়োগ করলে উদ্ভিদের স্বাভাবিক পুষ্প
প্রস্ফুটন ঘটে। বিভিন্ন উদ্দীপক- যেমন আলো, অভিকর্ষ ইত্যাদি উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। এভাবেই উদ্ভিদ তার
শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে সমম্বয় ঘটায়।
উদ্ভিদের চলন : উদ্ভিদ অন্যান্য জীবের ন্যায় অনুভূতি ক্ষমতাসম্পন্ন। এজন্য অভ্যন্তরীণ বা বহিঃউদ্দীপক উদ্ভিদ দেহে যে
উদ্দীপনা সৃষ্টি করে তার ফলে উদ্ভিদে চলন সংঘটিত হয়। কতকগুলো চলন উদ্ভিদ দেহের বৃদ্ধিজনিত আবার কিছু চলন
অভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক উদ্দীপকের প্রভাবে হয়। চলন যেভাকেই হোক না কেন তা অবশ্যই কোন না কোন প্রভাবকের
কারণেই ঘটে। উদ্ভিদ চলনকে প্রধানত দু’ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- সামগ্রিক চলন (গড়াবসবহঃ ড়ভ ষড়পড়সড়ঃরড়হ) ও
বক্রচলন।
সামগ্রিক চলন- উদ্ভিদ দেহের কোনও অংশ যখন সামগ্রিকভাবে প্রয়োজনের তাগিদে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে
তাকে সামগ্রিক চলন বলা হয়। যেমন- ছত্রাক ও উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদের জুস্পোরে এবং যৌন জনন কোষে এ ধরনের চলন
দেখা যায়। তাছাড়া অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়া ও কিছু শৈবালে যেমন- ঠড়ষাড়ী, ঈযষধসুফড়সড়হধং ও উরধঃড়স
(ডায়াটম) শৈবালেও এ ধরনের চলন পরিলক্ষিত হয়।
বক্র চলন- অন্যদিকে মাটিতে আবদ্ধ উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদ একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলাচল করতে পারে না। তবে
প্রয়োজনে এদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে চালনা করতে পারে ফলে অঙ্গগুলো নানাভাবে এঁকে বেঁকে অগ্রসর হয়। এ ধরনের চলনকে
বক্র চলন বলা হয়। কান্ডের আলোকমুখী চলন, মূলের অন্ধকারমুখী চলন, আকর্ষীর অবলম্বনকে পেঁচিয়ে ধরা ইত্যাদি বক্র
চলনের উদাহরণ।
সামগ্রিক চলন ও বক্রচলন আবার নানা ধরনের হয়। তারমধ্যে ফটোট্রপিক চলন উল্লেখযোগ্য। এ সম্পর্কে সংক্ষেপে নি¤েœ
বর্ণনা করা হলোফটোট্রপিক চলন- একে ফটোট্রপিজমও বলা হয়। এটি এক প্রকার বক্র চলন। সব সময় উদ্ভিদের কান্ড ও শাখা-প্রশাখার
আলোর দিকে চলন ঘটে। অপরদিকে মূলের চলন সব সময় আলোর বিপরীত দিকে হয়। কান্ডের আলোর দিকে চলনকে
পজিটিভ ফটোট্রপিজম এবং মূলের আলোর বিপরীত দিকে চলনকে নেগেটিভ ফটোট্রপিজম বলা হয়